স্মৃতির গর্জন ও বিবেকের দায়

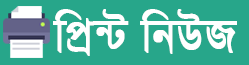
চব্বিশের জুলাই। ৩১ দিনে নয়, শেষ হয়েছিল ৩৬ দিনে। সেই উত্তাল সময় তৈরি করেছে নানা আনন্দের স্মৃতি ও বেদনার ক্ষত। তৈরি হয়েছে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। কেউ কেউ জীবনের পরোয়া না করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন সে সময়। কেউ পানি দিয়েছিলেন, কেউ আহত ব্যক্তিদের নিজের রিকশায় নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। কেউ খাবার দিয়েছিলেন। কেউ আন্দোলনকারীদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন বাড়ির দরজা। এমন অসংখ্য ঘটনা তৈরি করেছিল ‘৩৬’ দিনের দীর্ঘ জুলাই মাস। সে সময় সহপাঠীদের বাঁচাতে পুলিশ ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন নুসরাত জাহান টুম্পা। আর বাড়ির গ্যারেজে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দিয়েছিলেন অর্থী জুখরীফ।
এক বছর পর কী ভাবছেন তাঁরা?

এক বছর পেছনে তাকালে খানিকটা অবাক হই
অর্থী জুখরীফ, চিকিৎসক
সেদিনের কথা মনে পড়লে বেদনা, আতঙ্ক, গর্ব—সব একসঙ্গে ভিড় করে। আমি একদিকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম শিক্ষার্থীদের ওপর গুলির শব্দে। অন্যদিকে দায়িত্ববোধ থেকে গ্যারেজ খুলে দিয়েছিলাম সবার জন্য। আজ মনে হয়, সেদিন আমরা কেবল শরীর নয়, মনকেও সেবা দিয়েছিলাম।
এক বছর পেছনে ফিরে তাকালে আমি খানিকটা অবাক হই। কারণ, এটি ছিল আমাদের সব শ্রেণি, পেশা ও বিশ্বাসের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে গঠিত এক মানবিক অভ্যুত্থান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই অভ্যুত্থানকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক করে তোলা হচ্ছে। এতে আসল যে মানবিক শক্তির জাগরণ হয়েছিল, তা কিছুটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে। আমরা যাঁরা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই, কেবল বিবেকের তাড়নায় পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তাঁদের অবস্থানও হারিয়ে যাচ্ছে।
আমি চাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই দিনটি মনে রাখুক এক মানবিক জাগরণের দিন হিসেবে, যেখানে বিভাজনের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। যেন তারা শেখে, সাহস আর সহমর্মিতার গল্প কখনো পুরোনো হয় না। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই অভ্যুত্থানে নারীরা যেভাবে সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পূর্ণ স্বীকৃতি এখনো তাঁরা পাননি। বাস্তবে এই আন্দোলনে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অবদান ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যম ও আলোচনায় নারীদের উপস্থিতি অনেকটাই মুছে গেছে। যেন হঠাৎ করেই তাঁরা হারিয়ে গেলেন ইতিহাস থেকে। এটি কেবল অন্যায় নয়, ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তিকর। একজন মানুষ হিসেবে আমার মনে হয়, স্বীকৃতি কখনোই জেন্ডারভিত্তিক হওয়া উচিত নয়; মানবিকতা ও ত্যাগই হওয়া উচিত মূল্যায়নের মানদণ্ড।

চব্বিশে যে ঐক্যটা ছিল মানুষের মধ্যে, সেটা আর নেই
নুসরাত জাহান টুম্পা, শিক্ষার্থী
যে সময়টা আমরা পার করছি, সেটা আমাদের কাম্য ছিল না। আগে যেমন এলোমেলো হতো, এখনো তেমনই আছে। দেশে আইনের প্রয়োগ নেই, মানুষের মধ্যে দেশের জন্য কিছু করতে চাওয়ার ইচ্ছাটা আর নেই। যে যার নিজের মতো আখের গোছাচ্ছে। চব্বিশে যে একতা ছিল মানুষের মধ্যে, সেটা আর নেই। যাদের আমরা ওই সময়ে বিশ্বাস করতাম, এখন তাদের নেতিবাচক সমালোচনা করছি।
বরাবর আমাদের দেশে নারীদের ‘প্রয়োজন’ হলেই শুধু ব্যবহার করা হয়েছে। আন্দোলনের সময়টাতে ব্যবহার হয়েছে বলব না। কিন্তু তখন যতটা অ্যাপ্রিশিয়েট করা হয়েছে, এখন ততটা করা হচ্ছে না। দায়িত্ব দেওয়ার সময় এলে দেখা গেছে নতুন একটা দল গঠন করা হলো, যেখানে মূল নেতৃত্বের তালিকায় ১০ জনে মাত্র ২ জন নারী। আন্দোলনের পর যখন নারীরা নিজেদের মেলে ধরতে চাচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষেরাই তাকে বুলিং করছে। সামাজিকভাবে সেই স্বীকৃতিটা দিতে পারছি না নারীদের।
আমি নিজেকে ক্ষুব্ধ বলব না। একটা হতাশার জায়গা তো আছেই। আগে ভাবতাম, দেশের কিছুই হবে না। কিন্তু আন্দোলনের সময়টাতে আমি নিজের মানসিকতা বদলেছি। গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমার মনে পরিবর্তন এসেছিল। একটা আশার আলো দেখেছিলাম। এখন দেখি দেশে কী হচ্ছে, কারা কী বলছে,
দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। আমাদের দেশের ক্ষমতার চেয়ারটা কেমন জানি। সেখানে গেলেই মনে হয় মানুষ বদলে যায়। আমাদের দেশের সিস্টেম তখনই বদলাবে, যখন আমরা মানুষ হিসেবে নিজেকে বদলে ফেলতে পারব। আমাদের নিজের বিবেক, বোধ-বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। ভালো-খারাপ বুঝতে হবে। চব্বিশের আন্দোলনে দেশের কাঠামো বদলানোর কথা ছিল, সংবিধানে পরিবর্তন আনার কথা ছিল; বিশেষ করে আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো বদলানোর কথা ছিল। কিন্তু আমরা ঘুরেফিরে সেই একই কাঠামোর মধ্যে ঢুকে পড়েছি।




