রাশিয়ার নাকের ডগায় মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন, স্নায়ুযুদ্ধ ২.০ কি শুরু
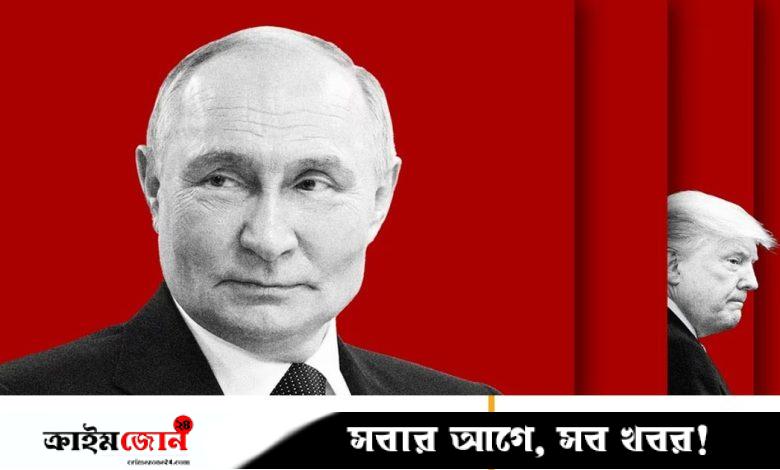
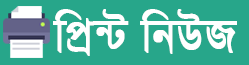
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কে উত্তেজনা গত কয়েক বছরে নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে, ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া উত্তেজনা এখন শুধু সামরিক বা কূটনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার মঞ্চেও। এমন প্রেক্ষাপটে অনেকেই প্রশ্ন করছেন—নতুন কোনো কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ ২.০ কি দরজায় কড়া নাড়ছে?
সম্প্রতি সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব দিমিত্রি মেদভেদেভের উত্তেজনাকর মন্তব্যের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুটি নিউক্লিয়ার সাবমেরিন রাশিয়ার উপকূলে মোতায়েনের নির্দেশ দিলে পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়েছে। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ এক ধরনের কৌশলগত সংকেত—যার উদ্দেশ্য রাশিয়াকে ভয় দেখানো, সরাসরি যুদ্ধ নয়। তবে দুই পরাশক্তির মধ্যকার উত্তেজনাকে স্নায়ুযুদ্ধের কল্পনায় রূপ দিতে এই ইঙ্গিত যথেষ্ট।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের এই সম্পর্কের টানাপোড়েন সরাসরি আগের স্নায়ুযুদ্ধের মতো নয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছিল—একদিকে মার্কিন পুঁজিবাদ, অন্যদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। কিন্তু বর্তমান দ্বন্দ্বের পেছনে মূলত কৌশলগত আধিপত্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা কাজ করছে।
কিংস কলেজ অব লন্ডনের অধ্যাপক ও বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ লরেন্স ফ্রিডম্যান যেমনটি বলেছেন, বর্তমান উত্তেজনাকে ‘স্নায়ুযুদ্ধ ২.০’ বলা যেতে পারে। তবে তাঁর মতে, এটি কোনো ভাবেই প্রথম স্নায়ুযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি নয়। কারণ আজকের রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পরাশক্তি নয়, বরং অর্থনীতি ও প্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে থাকা একটি দেশ।
ফ্রিডম্যান বলেন, ‘পারমাণবিক শক্তির ওপর জোর দেওয়া—দুই স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে একটি বড় মিল। তবে স্নায়ুযুদ্ধ ১.০ এবং ২.০–এর মধ্যে পার্থক্যগুলো অত্যন্ত গভীর। সবচেয়ে স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো—রাশিয়া এখন অনেক দুর্বল অবস্থানে রয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায়।’
তাঁর মতে, প্রথম স্নায়ুযুদ্ধ ছিল এক বৈশ্বিক ব্যাপার। যদিও এটি ইউরোপে শুরু হয়েছিল, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায়। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ ২.০–এ রাশিয়ার মনোযোগ মূলত ইউরোপেই কেন্দ্রীভূত। সিরিয়া এর ব্যতিক্রম হিসেবে একটি বড় উদাহরণ। তিনি বলেন, ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে রাশিয়ান ফেডারেশনে রূপ নেওয়ার ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে। প্রথম স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ব্লকের অর্থনীতির সঙ্গে বাকি বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পর্ক খুবই সীমিত ছিল, জ্বালানি খাত ছাড়া।’
বর্তমানে চলমান স্নায়ুযুদ্ধ ২.০—এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, মস্কো আর কোনো আন্তর্জাতিক আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দাবি করে না। স্নায়ুযুদ্ধ ১.০ ছিল ইন্টারনেট-পূর্ব যুগের দ্বন্দ্ব। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ ২.০–এর অবয়ব তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটের প্রভাবের মধ্য দিয়ে।
তবে রাশিয়ার এই ‘পিছিয়ে থাকাকে’ অবমূল্যায়ন করার সুযোগ নেই। বর্তমানে রাশিয়া, চীন, ইরান ও উত্তর কোরিয়া মিলে একটি অঘোষিত বৈশ্বিক অক্ষ গঠন করছে, যাকে পশ্চিমাদের অনেকে বলছেন ‘Axis of Upheaval’ বা ‘বিপর্যয়ের অক্ষ।’ এই জোটের লক্ষ্য পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়া নিজেকে ইউরোপ ও পশ্চিমের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কৌশলগত বিভ্রান্তি, যা রাশিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করছে।
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দূত ও পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক জন বোলটন এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ধাঁচের বিচ্ছিন্ন কৌশল বড় কোনো বৈশ্বিক লক্ষ্য তৈরি করতে পারছে না, বরং মার্কিন নেতৃত্বকে দুর্বল করছে। এর ফলে রাশিয়া ও চীন প্রভাব বাড়াতে পারছে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়।
জন বোলটনের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে পড়ে তখন পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা অনিশ্চয়তা ছিল—কী ঘটতে যাচ্ছে। সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ বলেছিলেন ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থার’ কথা। সে সময় মার্কিনরা ভেবেছিল, দুনিয়াজুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। কিন্তু তা আর হয়নি। অবশ্য, মার্কিনরা যেমনটা মনে করেছিল, রাশিয়া তাদের চাহিদামতো ‘ভালো হয়ে যাবে’ সেটাও হয়নি।
মার্কিন এই কূটনীতিক বলেন, ‘আরব দুনিয়ায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তা আমরা আগেভাগে টের পাইনি। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব কীভাবে পুরো অঞ্চলে “চরমপন্থার” বিস্তার ঘটাবে, সেটাও আঁচ করতে পারিনি। আবার ১৯৯০-এর দশকে আমরা চিন্তাও করিনি যে, চীন ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে উঠবে। আমরা শুনেছিলাম, দেং জিয়াওপিং চীনাদের বলেছিলেন, “তোমাদের ক্ষমতা লুকিয়ে রাখো, সময়ের অপেক্ষা করো।” আমরা বুঝতেই পারিনি উনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।’
ফলে, আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাশিয়া-চীন বলয়মুখী হওয়া, ব্রিকসের মতো জোটের মাধ্যমে পশ্চিমা আরোপিত বিশ্বব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করার আলোকে জন বোলটন মনে করছেন, ‘স্নায়ুযুদ্ধের অবসান মানেই ইতিহাসের অবসান, সংঘাত আর আমাদের জন্য আর কোনো হুমকি নয়—এই ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের বড় ভুল করতে বাধ্য করেছে। রাশিয়া, চীন এবং ইসলামি জঙ্গিবাদের হুমকি সম্পর্কে আমরা ভুল হিসাব করেছি।’
অন্যদিকে রুশ অর্থনীতিও এই উত্তেজনার মূল্য দিচ্ছে। রয়টার্সের এক সমীক্ষা বলছে, রুশ মুদ্রা রুবল আগামী ১২ মাসে প্রায় ২০ শতাংশ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা, আমদানি সংকট ও পুঁজিবাজারে অস্থিরতা এর কারণ। তবে এই আর্থিক চাপ রাশিয়াকে থামাতে পারেনি। বরং, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একপ্রকার ‘ঘাতসহ’ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছেন—যা তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনার মধ্যেও টিকে থাকতে দিচ্ছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই স্নায়ুযুদ্ধ যদি সত্যিই শুরু হয়ে থাকে, তবে তা আগের মতো কেবল পারমাণবিক অস্ত্র প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা নয়। বরং এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও সাইবার যুদ্ধকৌশল—এই নতুন ক্ষেত্রগুলোতে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিএসআইএস বলছে, ১৯৮০-এর দশকে মার্কিন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে বড় ভূমিকা রেখেছিল। আজকের দিনে সেই প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা আরও তীব্র, আরও বহুমাত্রিক। এখন শুধু অস্ত্র তৈরি নয়, বরং তথ্যপ্রবাহ, বাণিজ্য নেটওয়ার্ক, এমনকি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দিকেও নজর দিতে হচ্ছে।
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বন্দ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি আর এই উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আইএনএফ বা স্টার্ট—এর মতো কৌশলগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলো কার্যত অকার্যকর হয়ে গেছে। নতুন কোনো চুক্তির সম্ভাবনাও নেই। এর ফলে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা একটি অস্থির, অপ্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।
এমন পরিস্থিতিতে নতুন স্নায়ুযুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, এই দ্বন্দ্ব ‘প্রক্সি যুদ্ধের’ মাধ্যমে চলবে—যেমনটা এখন ইউক্রেনে হচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, এই স্নায়ুযুদ্ধ হবে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির মাঠে—যেখানে এআই চালিত অস্ত্র, ডিজিটাল মুদ্রা ও ব্লকচেইন নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম মূল যুদ্ধক্ষেত্র।
তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো—এই উত্তেজনার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই। আগে যেমন পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত বিশ্বে দুই পরাশক্তির একটি সুস্পষ্ট বিরোধ রেখা ছিল, এখন তেমন নেই। ফলে ছোট কোনো ভুল পদক্ষেপ, ভুল তথ্য বা রাজনৈতিক হঠকারিতাই বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নিতে পারে।
তবে দ্বিমুখী একটি স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে এমনটা মনে করেন না হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অড আর্নে ওয়েস্ট্যাড। তাঁর মতে, ‘আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্নায়ুযুদ্ধের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। আগের মতো দ্বিধাবিভক্ত (বাইপোলার) বিশ্ব আর নেই…চীন ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে…রাশিয়া বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক অতৃপ্ত সুযোগসন্ধানী…মতাদর্শ এখন আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান চালিকাশক্তি নয়।’
চীন, ইউরোপ, ভারত, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র অনেক বিষয়েই একমত নয়, তবে পুঁজিবাদ ও বাজারব্যবস্থার মূল্য নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ নেই। চীন ও রাশিয়া—উভয়ই কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র, যারা নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার ভান করে। তবে তারা আর আগের মতো তাদের শাসনব্যবস্থা অন্যত্র রপ্তানি করতে চায় না, যেমনটা তারা স্নায়ুযুদ্ধের সময় করত। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র—যে দেশ অতীতে রাজনৈতিক মূল্যবোধ রপ্তানি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল—ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির অধীনে এখন তা থেকেও অনেকটা পিছিয়ে এসেছে।
ওয়েস্ট্যাড বলেন, ‘বর্তমানে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, তা স্নায়ুযুদ্ধ নয়…ইতিহাসকে যদি আমরা নীতিনির্ধারণে কাজে লাগাতে চাই, তাহলে আমাদের সাদৃশ্য খোঁজার পাশাপাশি পার্থক্যগুলো সম্পর্কেও সমানভাবে সচেতন থাকতে হবে।’
এ অবস্থায় বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুদ্ধ নয়—বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতি, অভ্যন্তরীণ সংহতি এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ হুমকি মোকাবিলা করতে হবে। ইউরোপের দেশগুলোর উচিত হবে নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানো, যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্বে স্থির থাকা, আর রাশিয়ার মতো দেশকে কূটনৈতিক চাপে রেখে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অন্যদিকে রাশিয়ার লক্ষ্য থাকবে—যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব যেন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নতজানু হয়ে পড়ে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, বিশ্ব এক ধরনের স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যেই আছে—যার রূপ, মাত্রা ও কৌশল আগের চেয়ে আলাদা, তবে পরিণতি কতটা গভীর হবে, তা নির্ভর করছে বিশ্বনেতাদের বিচক্ষণতা ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের ওপর।
এ বিষয়ে কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের গবেষক ইউজিন রুমার বলেন, ‘আমাদের বুঝতে হবে কীভাবে আমরা রাশিয়াকে গত পঁচিশ বছরে বহুবার অংশীদার বলে ঘোষণা করার পরও শেষমেশ তার সঙ্গে একটি নতুন স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম। আমাদের নিজেদের অতীত কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে—আমরা সবকিছু ঠিকভাবে করেছি কি না, কোনো ভুল করেছি কি না, আর ভবিষ্যতে সেই ভুলগুলো কীভাবে এড়িয়ে চলা যায়।’
তথ্যসূত্র: বিজনেস ইনসাইডার, ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট, দ্য আটলান্টিক ও রাশিয়া ম্যাটারস




