গবেষণাগারে ‘ব্ল্যাকহোল বোমা’ তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা, প্রমাণিত হলো ৫০ বছরের পুরোনো তত্ত্ব
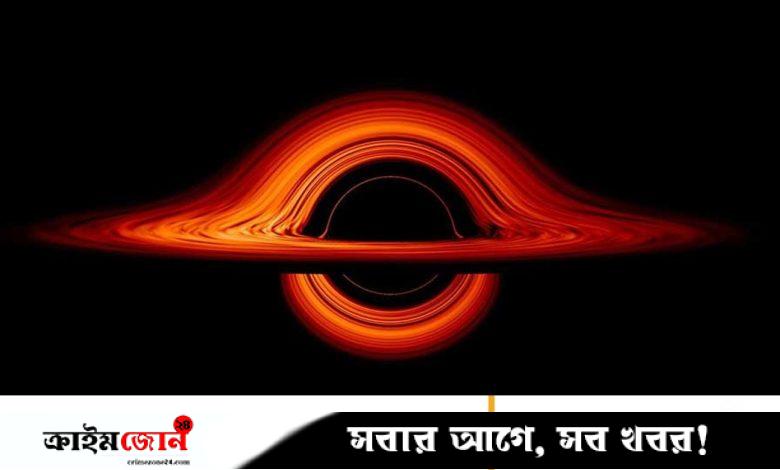
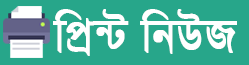
গবেষণাগারে প্রথমবারের মতো তৈরি হলো ‘ব্ল্যাকহোল বোমা’। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৫০ বছর আগের পুরোনো তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন একদল আন্তর্জাতিক গবেষক। প্রকৃত ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন ও নানা রহস্য বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এই গবেষণা।
১৯৭২ সালে একটি তাত্ত্বিক ঘটনা বর্ণনা করেন পদার্থবিদ উইলিয়াম প্রেস ও সল টেউকোলস্কি। এই তাত্ত্বিক ঘটনাকে বলা হয় ‘ব্ল্যাকহোল বোমা’। এ তত্ত্ব অনুসারে, ঘূর্ণমান ব্ল্যাকহোল থেকে নির্গত তরঙ্গ যদি আয়নাসদৃশ বস্তুর ভেতরে প্রতিফলিত হয়, তাহলে তা বারবার প্রতিফলিত হয়ে শক্তি ও ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ, একধরনের বোমায় পরিণত হয়।
সম্প্রতি এই তত্ত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব সাউদাম্পটন, ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগো এবং ইতালির ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের ইনস্টিটিউট ফর ফোটোনিকস অ্যান্ড ন্যানোটেকনোলজির বিজ্ঞানীরা। গত ৩১ মার্চ ‘অ্যারএক্সিভ’ প্রিপ্রিন্ট সার্ভারে প্রকাশিত হয়েছে গবেষণাপত্রটি। তবে এটি এখনো পিয়ার-রিভিউ হয়নি।
ব্ল্যাকহোল বোমার ধারণা আসে আগের আরেক তত্ত্ব থেকে। ১৯৬৯ সালে ঘূর্ণমান ব্ল্যাকহোল থেকে শক্তি আহরণের পদ্ধতি প্রস্তাব করেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ ও নোবেলজয়ী স্যার রজার পেনরোজ। এই তত্ত্ব ‘ব্ল্যাকহোল সুপাররেডিয়েন্স’ নামে পরিচিত।
এরপর ১৯৭১ সালে বেলারুশের পদার্থবিদ ইয়াকভ জেলদোভিচ ঘটনাটি আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পারেন, সঠিক পরিস্থিতিতে, একটি ঘূর্ণমান বস্তু তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে আরও শক্তিশালী করে করতে পারে। এ ঘটনাই ‘জেলদোভিচ এফেক্ট’ নামে পরিচিত।
নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জেলদোভিচ এফেক্ট ব্যবহার করেই পরীক্ষা চালান। গবেষকেরা অ্যালুমিনিয়ামের সিলিন্ডারকে একটি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঘোরান। চারপাশে তিন স্তরের ধাতব কুণ্ডলী বসিয়ে একটি চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি এবং সিলিন্ডারে প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়। এই কুণ্ডলীগুলো আয়নার মতো কাজ করে।
প্রথমে একটি দুর্বল চৌম্বক তরঙ্গ সিলিন্ডারের দিকে পাঠানো হয়। দেখা যায়, সিলিন্ডার যে চৌম্বক তরঙ্গ ফেরত পাঠাচ্ছে, তা আরও বেশি শক্তিশালী। এটি সুপাররেডিয়েন্সের প্রমাণ।
পরবর্তী ধাপে গবেষকেরা কুণ্ডলী থেকে প্রাথমিকভাবে তৈরি করা দুর্বল চৌম্বকক্ষেত্রটি সরিয়ে ফেলেন। এর পরও সার্কিট নিজেই তরঙ্গ তৈরি করতে থাকে এবং ঘূর্ণমান সিলিন্ডার তা আরও শক্তিশালী করে তোলে। ফলে কুণ্ডলীগুলোর মধ্যে শক্তি জমা হতে থাকে।
জেলদোভিচের পূর্বাভাস অনুযায়ী, যদি কোনো বস্তু এত জোরে ঘোরে যে, তার গতি ওই বস্তুর দিকে আসা তরঙ্গের চেয়েও বেশি হয়, তাহলে বস্তুটি আর সেই তরঙ্গকে শোষণ করে না। বরং সেই তরঙ্গকে আরও শক্তিশালী করে ফেরত পাঠায়। জেলদোভিচের এই তত্ত্ব গবেষণায় প্রমাণিত হয়।
গবেষণার সহলেখক ইউনিভার্সিটি অব সাউথহ্যাম্পটনের গবেষক ম্যারিয়ন ক্রম্ব বলেন, ‘কখনো কখনো আমরা সিস্টেমে এত বেশি চাপ দিয়েছি যে সার্কিটের উপাদানগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। সেটা ছিল একই সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ এবং একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ!’
যদিও গবেষকেরা আসল কোনো ব্ল্যাকহোল তৈরি করেননি। তবে এ গবেষণা প্রমাণ করে যে, রোটেশনাল সুপাররেডিয়েন্স ও এক্সপোনেনশিয়াল অ্যামপ্লিফিকেশন কেবল ব্ল্যাকহোলেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা।
গবেষণার আরেক সহলেখক ও ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর পদার্থবিদ কিয়ারা ব্রাইডোত্তির জানান, এই মডেল কেবল ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন নয়, বরং জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাপগতিবিদ্যা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সংযোগস্থলে থাকা বহু জটিল তত্ত্ব বোঝাতেও বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে।




