সবার অভিন্ন লক্ষ্য ছিল স্বৈরতন্ত্রের পতন

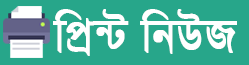
টানা তিনটি জাতীয় নির্বাচনে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং দমনপীড়নের নির্লজ্জ রূপ প্রদর্শন করে ১৫ বছর ৭ মাস প্রধানমন্ত্রিত্ব ধরে রাখার মাধ্যমে শেখ হাসিনা বিশ্বের অন্যতম নিকৃষ্ট স্বৈরাচারী শাসকদের কাতারে নিজের অবস্থান পাকা করেছিলেন। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তাঁর অনুগত বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এক বছর আগে, ঠিক এই দিনে তিনি পদত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভারতে চলে যান। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) একটি গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়, সেদিনই গণভবন, সংসদ ভবনসহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় তাঁর ও পরিবারের নিরাপত্তায় থাকা এসএসএফ সদস্যদের অস্ত্র ও সরঞ্জাম লুট হয়ে যায়। (সূত্র: ইত্তেফাক, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)
জনতার ক্ষোভের মাত্রা বোঝাতে এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট নয়; জুলাই ও আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনের আন্দোলনে হতাহতের পরিসংখ্যান এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে জনগণ আর চুপ থাকার অবস্থায় ছিল না। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য কোটা পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের আদেশের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ১ জুলাই রাজপথে নামেন। ১৪ জুলাই শেখ হাসিনা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতি বিদ্রূপ মন্তব্য করেন, ‘মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা না পেলে রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?’ ওই রাতেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্রী হলের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে স্লোগান তোলেন—‘তুমি কে, আমি কে? রাজাকার রাজাকার!’; ‘কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।’
পরদিন ছাত্রলীগ সশস্ত্র হামলা চালায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর, যেখান থেকে সহিংসতার সূচনা। ১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে শহীদ হন ওয়াসিম আকরাম। সেদিন পাঁচ শিক্ষার্থী শহীদ হন। এরপর সরকার এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন যৌথভাবে রক্তক্ষয়ী দমনপীড়ন চালায়। কারফিউ দিয়ে, ইন্টারনেট বন্ধ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করে, ব্লক রেইডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তারসহ নানা অপারেশন পরিচালনা করে তারা।
জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে দলীয় সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে। ওই প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০। অন্যান্য হিসাবে আহত ১০ হাজারের বেশি। পাঁচ শতাধিক মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, ১৩৩টি শিশুর প্রাণ গেছে। সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন শ্রমজীবীরা। তবু মানুষ রাজপথ ছাড়েনি; শহীদদের দাফন করে তারা আবার বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে। কবির ভাষায়, ‘জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি টালমাটাল’। এটি এক অপ্রতিরোধ্য সত্যে পরিণত হয়েছে।
১৯ জুলাই ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ৯ দফা দাবি পেশ করে। এরপর আন্দোলনের পরিধি বাড়তে থাকে। ঢাকার অলিগলি ও জেলাগুলোয় সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমজীবী, অভিভাবক সবাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্ম হয়। ৩ আগস্ট ঘোষণা আসে এক দফা—শেখ হাসিনার পদত্যাগ। এই এক দফাকে ঘিরে গড়ে ওঠে জাতীয় ঐক্য, যা অবশেষে বিভিন্ন মতাদর্শের দলগুলোকে একত্র করে, এমনকি ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যে বামপন্থীরা দেড় দশক ধরে কোনো ধরনের আন্দোলনে শামিল হতে চায়নি, সেই অসম্ভবকেও সম্ভব হতে দেখা যায়।
স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনের যে প্রত্যাশা, তা তরুণ প্রজন্মের ওপর নির্ভরশীল। অনেকে একে বলছেন, ‘বাংলাদেশ ২.০’। কিন্তু এই নতুন বাংলাদেশের রূপ কেমন হবে, সে প্রশ্ন এখনো উন্মুক্ত। স্বপ্নদ্রষ্টা তরুণ, নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী কিংবা নৈরাজ্যবাদী—সবার অভিন্ন লক্ষ্য ছিল স্বৈরতন্ত্রের পতন; কিন্তু তার স্থলে কী আসবে, সে বিষয়ে ঐক্য তখনো ছিল না, এখনো বহুলাংশে অনুপস্থিত।
এই অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠিত হয়, যারা ৪৫ দিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পৃথকভাবে এবং ২৩ দিন সর্বদলীয় আলোচনায় সময় ব্যয় করেছে। যে রাজনীতিকেরা এক টেবিলে বসতে রাজি ছিলেন না, তাঁরা আজ ৯টি মূল বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং অন্যান্য বিষয়ে মতপার্থক্য কমিয়ে এনেছেন; এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। তবে বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, যা সময়সাপেক্ষ।
জনগণের ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। এই হতাশার পেছনে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু দায় রয়েছে। গত এক বছরে সরকার অনেক কিছু করতে চেয়েছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ যথাযথ ছিল না। যেসব ক্ষেত্রে উপদেষ্টারা তাঁদের ব্যতিক্রমী কাজে সফল হয়েছেন, সেগুলোর সুফল দৃশ্যমান নয় বা তাঁরা তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপদেষ্টাদের অনেককে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়, যা জন-আস্থার সংকট বাড়িয়ে তুলেছে।
১৮ কোটি মানুষের দেশে অপ্রত্যাশিত ঘটনা অসম্ভব নয়। কিন্তু যখন সরকার প্রতিক্রিয়াহীন, অপ্রস্তুত কিংবা দর্শকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়, তখন সবাই তার পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে যে তুলনা টানবে, সেটি স্বাভাবিক। বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানের পর তাই প্রয়োজন হয় দৃঢ় ও দক্ষ নেতৃত্ব। কেননা মানুষ নেতৃত্বের মধ্যে দক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করে।
সে কারণে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চলমান প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই ধারা এগিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ সার্থক হবে।




